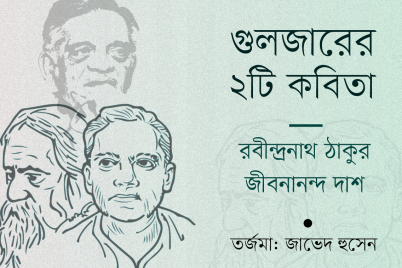(৫)
সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি ফেলে রেখে একটা ছই দেওয়া গরুর গাড়িতে উঠে গজেন্দ্রনাথ চলে এসেছিল পাঁচ কিলোমিটার দূরে পরিষ্কার একটি জায়গায়,যা ভবিষ্যতে একটি মফস্বলী নগর হয়ে উঠার সম্ভাবনা বহন করছিল। গরুর গাড়িটার ছৈ দেওয়া ছায়ার নিচে কিছু আসবাবপত্রের মধ্যে প্রায় চ্যাপ্টা হয়ে দুলে দুলে আসছিল গজেন্দ্রনাথের বাঁ পাশে বসে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী অমৃতপ্রভা। উড়নার নিচে অমৃতপ্রভা সামনের দিকে তাকানোর জন্য চেষ্টা করলেই গাড়োয়ানের উদম পিঠটা দেখতে পায়, যেখানে ভবিষ্যতের কোনো চিহ্ন ছিল না। সে ভেবেছিল সেই পিঠের ওপাশে গজেন্দ্রনাথের স্বপ্নগুলির হাত ধরে গড়ে উঠবে তার ভবিষ্যৎ।
আর ভবিষ্যৎ ছিল একটা বেলগাছের নিচে। সেখানে গজেন্দ্রনাথ একটা চায়ের দোকান আরম্ভ করেছিল। একটা হলঘরের মতো প্রকাণ্ড ছিল ‘বেলের নিচের চায়ের দোকান’। হলঘরটির দুপাশের দীর্ঘ বেড়া দুটির গা ঘেঁষে পেতে রাখা ছিল লম্বা লম্বা বেঞ্চ। আর বেঞ্চগুলির সামনে লম্বা লম্বা ডেস্ক। ডেস্কগুলি ছিল অ্যালুমিনিয়ামের পেরেক মারা। সেখানে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে না। জ্যোৎস্না সেখানে পড়ে জ্বলজ্বল করতে কতই না ভালোবাসত।
ভাঁজে ভাঁজে খুলে রাখতে পারা প্রকাণ্ড মুখের দুটি দরজা ছিল বেলের নিচের চায়ের দোকানের, হাতে ধরাধরি করে পাঁচ-ছয় জন তার মধ্য দিয়ে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারার মতো। হলঘরটার এককোণে ছিল একটি বিশাল কাঠের খাট। তার ওপরে মোটা তোশক। তার ওপরে একটা সাদা কাপড়,পবিত্রতার। খাটটার পাশ দিয়ে উপরে উঠে গেছে একটি শাল কাঠের মোটা খুঁটি। খুঁটিটার গায়ে পেরেক মেরে রাখা আছে তেল-চিটে কালো হয়ে পড়া ত্রিভুজাকৃ্তি খোলা বাক্স। তার মধ্যে বাণিজ্য দেবতা থাকে। বাণিজ্য দেবতার মাথাটা হাতির বলে, সেই দেবতার মুখের কোনো অভিব্যক্তি বোঝা যায় না-তিনি সন্তুষ্ট না আহত! সাদা ধবধবে খাটার ওপরে থাকে দোকানটার মূল্যবান জিনিসটা-পয়সা রাখার জন্য একটা বাক্স। বাক্সটার ভেতরে থাকে অনেকগুলি তাক, তার থাকে থাকে রাখা হয় টাকা পয়সা। কোনোটাতে থাকে সবচেয়ে বড়ো নোটগুলি,দশ টাকা। কোনোটাতে আধুলি। কোনোটাতে সিকি (২৫ পয়সা) দশ পয়শা,পাঁচ পয়শা, দুই পয়শা, এক পয়শার বাসস্থান ছিল একসঙ্গে। বাক্সটাতে একটা বাহু রেখে হেলান দিয়ে বসে থাকে গজেন্দ্রনাথ। সামনের প্রকাণ্ড দরজা দুটি দিয়ে তাঁর দৃষ্টি অনেক দূরে চলে যায়-সেখানে থাকে একটা ধান বানা কলের দীর্ঘ নিঃসঙ্গ চিমনি। চিমনিটার কালো ধোঁয়া আকাশে উড়ে যায় খুব ধীরে ধীরে এবং আকাশে তৈরি করে নেয় একটা কালো রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে একটা পক্ষী্রাজ ঘোড়া উড়ে যায়। পক্ষীরাজের পায়ে নূপুর। নূপুরের স্পষ্ট শব্দ গজেন্দ্রনাথের কানে আসে। গজেন্দ্রনাথের অন্য হাতে তখন চারপাঁচটা আধুলি লাফিয়ে লাফিয়ে ঝুনঝুন শব্দ করে!
একটা তীর্থস্থানের মতো ছিল ‘বেলের নিচের চায়ের দোকান’। তিনটি কারণে বিখ্যাত ছিল এই তীর্থস্থান। প্রথম–এই দোকানের মালিক অর্থাৎ গজেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন শক্তিশালী, পরোপকারী এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ, যিনি প্রতিদিন শালগ্রাম ধুয়ে দুধ দিয়ে পদজল খায়, ভূত–প্রেত যাকে ভয় করে, যার বিনামূল্যের তাবিজ পরলে অপদেবতা কাছে আসতে পারে না, যিনি মহিলাদের সাদাস্রাবের অসুখ মাত্র এক বোতল ওষুধ দিয়ে ভালো করে দিতে পারে…
দ্বিতীয় কারণ হল—এই দোকানের সুস্বাদু লবঙ্গ। আর তৃতীয় কারণ হল–’ বেলের নিচের চা দোকানে’ মুসলমান মানুষের প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানরা চা খেতে হলে বেলগাছের গায়ে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে রাখা কাপগুলি থেকে একটা কাপ নিজে তুলে নিতে হবে এবং সেখান থেকেই চিৎকার করবে বা ইঙ্গিত দিতে হবে যে তার চায়ের প্রয়োজন! তখন একটা চাকর উনুনের ওপরে থাকা কেটলিটা বাইরে বের করে এনে তার কাপে গরুর দুধের চায়ের কাপ ঢেলে দেবে আর জিজ্ঞেস করবে–’ লবঙ্গ দেব কি’?
বরফি খাওয়া একজন মুসলমানকে ওষুধ দিতেও দ্বিধা করছিল গজেন্দ্রনাথ। চাকরটির হাতে মুক্তির আনন্দে একটা লবঙ্গ উঠে এসে বেলের নিচে পৌঁছে মুসলমানের হাতে পড়বে। তারপর বড়ো তৃপ্তিতে মুসলমানের পেটে ঢুকবে গজেন্দ্রনাথের লবঙ্গ। চা-লবঙ্গ খেয়ে মুসলমান বাইরে থাকা একটা বালতির জলে কাপটা পরিষ্কার করে, সেই পেরেকটাতে পুনরায় ঝুলিয়ে রাখবে, যেখান থেকে সে তাকে নামিয়ে এনেছিল। তারপরে লুঙ্গির গিঁট খুলে মুসলমানটা চাকরের হাতে পয়সা দেবে ছয় ইঞ্চি ওপর থেকে।
যদি কোনো মুসলমান পায়জামা বা লংপ্যান্ট পরে বেল গাছের নিচে চায়ের দোকানে লবঙ্গ চা খেয়ে চলে যায়, যদি মানুষের খাওয়া বাসনের সঙ্গে মুসলমানের ঝুটা মিলে যায়?–তাহলে শঙ্কা বা দুশ্চিন্তা করার কিছুই ছিল না গজেন্দ্রনাথের (সেরকম শঙ্কা ছিল কেবল কিছু কুটিল গ্রাহকের), কারণ লংপ্যান্ট পায়জামা পরা মুসলমান থাকতে পারে বলে গজনেন্দ্রনাথ কল্পনাই করতে পারেনি। আর আত্মবিশ্বাসও ছিল গজনেন্দ্রনাথের যে কোনো মুসলমান সেরকম অন্যায় করে না। এত অকপট, এত সরল ছিল গজেন্দ্রনাথ।
(ছয়)
প্রত্যেকেই যে চায়ের সঙ্গে লবঙ্গ খেত এমন নয়। কিছুলোক বরফিও খেত। যারা বরফি খেত তাঁরা ছিল আপেক্ষিকভাবে ধনী এবং ধীর-স্থির, কিছুটা আভিজাত্যের রঙ মাখানো। গজেন্দ্রনাথের ধবধবে বিছানাটার একেবারে পাশের ডেস্ক-বেঞ্চে তারা বসেছিল। কিন্তু গজেন্দ্রনাথের লবঙ্গের তুলনা নেই। সমগ্র বজালী অঞ্চলেই কেন, বজালীর মধ্য দিয়ে বাস-ট্যাক্সি পার হয়ে যেতে চাওয়া মানুষগুলিও বেলের নিচের চায়ের দোকানের সামনে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করত। আর সাইকেল আরোহীদের তো কথাই নেই! ক্লান্ত হয়ে তারা প্রবেশ করত গজেন্দ্রনাথের চায়ের দোকানে এবং বেরিয়ে আসত সতেজ-সজীব হয়ে!
চায়ের দোকানটার কোনো নাম ছিল না। বেলগাছটার গায়ে ছোট একটি সাইনবোর্ড পেরেক মেরে রাখা ছিল। তাতে লেখা ছিল-‘লবঙ্গ চা খান, বাড়ি ফিরে যান।’
গজেন্দ্রনাথের বাড়িটা চায়ের দোকানের পেছনে একটা চৌহদ্দির মধ্যে ছিল। তাই বাড়ির প্রত্যেক সদস্যই সকাল এবং বিকেলের চা-জলখাবার দোকানটা থেকেই খেত। মহিলা এবং বয়স্করা -বয়স্ক বলতে কেবল ছিল রাহুলের পিতা-চায়ের দোকানে নিজে এসে খেত না। তাদের প্রত্যেকের সকাল এবং বিকেলের চায়ের ভাগটুকু বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাগ করে দেওয়া হত। তজো নামে ছোটোখাটো কিন্তু জনপ্রিয় চাকরটি সেই কাজটা করত। তজো কেন জনপ্রিয় ছিল বোঝা যায় না। বেলের নিচের চায়ের দোকানে কাজ করা ৮-১০টি ছেলের ভেতরে দেখতে সে কুশ্রী হয়েও কীভাবে জনপ্রিয় হতে পারল, সেই রহস্য পরে কখনও আবিস্কৃত হয় যদি হবে। রাহুলসহ বাকি ছেলে মেয়েরা সকাল-বিকেলের চা খাবার জন্য দোকানে এসে ডেস্ক-বেঞ্চে ঠিক গ্রাহকের মতো বসে পড়ত। ওদের সকাল-বিকেলের চা খাবার জন্য একটা ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়া হত। রাহুলরা সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে সেই ঘন্টাধ্বনির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওরা দৌড়ে গিয়ে একেবারে ওদের দাদুর দোকানে উপস্থিত হত, কী পবিত্র সেই ঘন্টাধ্বনি! গির্জাঘরের ঘণ্টাও যেন সেই ঘন্টার কাছে নিস্তেজ হয়ে যায়।
সকালের সেই সময়টুকু অর্থাৎ রাহুলরা চা খেতে আসা সময়টুকুতে দাদু গজেন্দ্রনাথ দোকানে থাকেন না। সেই সময়টুকু দোকানে কাজ করা ছেলেগুলির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে রেলের নিচের চায়ের দোকানে। সেই সময়টুকু গজেন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব সময়। দা নিয়ে তিনি বাগানে বেরিয়ে যান। ঢেঁকিয়া বাদ দিয়ে নাম এবং জাত-পাতহীন বন-লতা কাটেন। কোথাও বাঁশের ডাল একটা হেলে পড়ে কষ্ট পেতে দেখলে আগাটা কেটে দেন। খসে পড়ে থাকা সুপুরিগুলি কুড়িয়ে এনে উঠোনে রাখেন।তারপর গোয়ালঘরে নিয়ে যান।গোবরগুলি একটা টুকরিতে ভরিয়ে নিয়ে পান-সুপুরি গাছের গোড়ায় ঢেলে দেন। তখনই অমৃতপ্রভা হাতে ছোট একটি বালতি নিয়ে গোয়ালঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। গজেন্দ্রনাথ অমৃতপ্রভার হাত থেকে বালতিটা নিয়ে কাজলী গাইটার কাছে যায়। কাজলীর দুধ কম।তার দুধ দুইয়ে মুগীর কাছে যায়। অনেকক্ষণ তার পিঠে হাত দিয়ে আদর করেন গজেন্দ্রনাথ। কারণ মুগী ভীষণ মেজাজি।তার অনুমতি না পেলে তার দুধ দোওয়া যায় না। অনেক আদর-টাদর করে মুগীকে রাজি করাতে হয় এবং গজেন্দ্রনাথ পিতলের বালতিতে তুলে নিয়ে আসে দুই ধারায় নেমে আসা রূপালী ঝর্ণার ধারা। তারপর গজেন্দ্রনাথ অমৃতপ্রভার পরিষ্কার হাতটিতে বালতিটা তুলে দিয়ে স্নান করতে যায়। স্নান করে উঠে তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন, গায়ে গা লাগিয়ে যেখানে একটা ভাঁড়ার ঘর রয়েছে।
অন্ধকার অন্ধকার ভাব থাকা ঠাকুরঘরের মাটির মেঝেটা ইতিমধ্যে অমৃতপ্রভা মুছে রেখেছে। গজেন্দ্রনাথ সেই মেঝেতে পায়ের ছাপের স্পষ্ট দাগ বসিয়ে দেয়। বাঁশের একটা ধাড়িতে বসেন। কোষা-অর্ঘ্যে জল ঢালেন। মাটির প্রদীপটা জ্বালিয়ে দেন। তারপর সেই প্রদীপের আগুনে তিনটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দগ্ধ আর ছাই হওয়ার জন্য ছেড়ে দেন। তারপর অর্ঘ্য থেকে হাতের অঞ্জলিতে তিনবার জল নিয়ে বলেন-ওঁ ভূ স্বাহাঃ! ওঁ ভব স্বাহাঃ।ওঁ স্ব স্বাহাঃ।
আসন থেকে গজেন্দ্রনাথ নামিয়ে আনে গায়ে-মাথায় কাপড় নিয়ে শুয়ে থাকা ভগবানের মূর্তিগুলি। প্রথমে আনে সোনার মতো জ্বলজ্বল করতে থাকা গনেশকে, তারপর বাঁশি বাজাতে থাকা কৃ্ষ্ণকে, তারপরে কোনো ভাবমূর্তি না থাকা রাধাকে। সেটা রাধা না লক্ষ্মী বোঝা যায় না। কৃষ্ণের সঙ্গে কাপড়ের একই আসনে শোবার জন্য রাধা বলেই মনে হয়। কিন্তু রাহুলদের দাদু তাকে লক্ষ্মী বলে।
কালো পাথরের গোল লেবুটার সমান শালগ্রামশিলাটা বেশ শক্তিশালী এবং অভিমানী। একবার নাকি অভিমান করে শালগ্রামটা ভাঁড়ারের ভেতরে ধানগুলির মধ্যে শুয়ে ছিল। সেই শালগ্রামটার শরীরে আগের দিন থেকে লেপ্টে থাকা তুলসিপাতাটা সরিয়ে দিয়ে গজেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি ভগবানকে একটা বড়ো কাঁসিতে রাখে। আর প্রথমে অন্য ভগবানগুলিকে জল দিয়ে স্নান করিয়ে শেষে শালগ্রামশিলাকে শুধু দুধ দিয়ে স্নান করায়। শালগ্রামশিলা জল দিয়ে স্নান করে না কেন? শরীর কালো বলে ফর্সা হওয়ার ইচ্ছা কি?
স্নান করিয়ে, মুছে, পুনরায় গজেন্দ্রনাথ ভগবানগুলিকে আসনে দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে রাখে। এইবার গজেন্দ্রনাথ গোলাপ,করবী, ধুতরা এবং গাঢ় নীল অপরাজিতা,বেল্পাতা,তুলসিপাতা এবং দুব্বো দিয়ে ভগবানকে ঢেকে ফেলে।তুলসিপাতায় চন্দনের লেপ লাগিয়ে শালগ্রামশিলাটার বুকে লাগিয়ে দেয়। অবশ্য সেটাকে বুক বলা যায় না। একটা গোলাকার বস্তুর নির্দিষ্ট বুক খুঁজে বের করা সহজ নয়। ঘন্টা, শঙ্খ এবং বড়ো কাসির শব্দে গজেন্দ্রনাথের চারপাশ ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। এই সম্পূর্ণ কাজটুকু গোঁসাইঘরে গজেন্দ্রনাথ একা করতে ভালোবাসে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি ছোটো চাটাই পেতে রাহুল কাছে বসে থাকে, তখন গজেন্দ্রনাথ আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে থাকে।
গজেন্দ্রনাথের বিখ্যাত লবঙ্গ রাহুলরাও বিনা পরিশ্রমে সকাল বিকেল খেতে পেত। ওদের চা খাওয়ায় নিষেধ ছিল। ওদের দেওয়া হত চা তৈরি করার জন্য চাপাতা না দিয়ে উথলে রাখা দুধ এবং জলের মিশ্রণটা, যাকে সরবৎ বলা হত। কখনও লবঙ্গ খেতে ইচ্ছা না করলে জিলাপি, খুরমা বা মালপোয়া খাওয়ার অধিকার ছিল ওদের। কেবল অধিকার ছিল না বরফি খাওয়ার।
কাঁচের আলমারিটাতে লবঙ্গ-জিলাপিদের সঙ্গে বরফিও বন্দি হয়ে ছিল। বরফিগুলি ছিল আলমারিটার ওপরের খোপে দৌলের মতো সাজিয়ে রাখা। বিশেষ কারণে নিমকিগুলি সেখানে রাখা হত না। নিমকিগুলি ছিল বড়ো স্পর্শকাতর, একটু হাওয়া লাগলেই স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। তাই ওদেরকে নির্দয়ভাবে বন্দি করে রাখা হত টিনের বাক্সের মধ্যে, অন্ধকারের ঢাকনা লাগিয়ে।
মুখে দিলে গলে যাওয়া ধবধবে সাদা বরফিগুলির দাম ছিল লবঙ্গ বা তার সতীর্থদের চেয়ে দ্বিগুণ। তাই বিধিসম্মতভাবে রাহুলদের বাড়ির কোনো সদস্যেরই সেই বরফি খাওয়ার অনুমতি ছিল না। বরফি খেতে পেরেছিল তখন, যখন কোনো একজনের জ্বর হত নতুবা কোনো অজানা রোগে পড়ত, যে রোগে লবঙ্গ খেলে অন্যায় হবে বলে ভাবা হত।
কিন্তু বরফি খাওয়ার আরও একটি উপায় ছিল। সেই অবৈধ উপায় রাহুল জানত। কিন্তু সেটা কি একটা উপায় ছিল? না নিয়তির ষড়যন্ত্র?
বেলের নিচে চায়ের দোকানের সবচেয়ে বড়ো চাকরটি, যাকে অন্যেরা কিছুটা ভয় করে চলত-রাহুলকে জিজ্ঞেস করেছিল-বরফি খাবি?’
‘খাব।’ রাহুল চট করে উত্তর দিয়েছিল। ‘তাহলে এটা নাড়াতে থাক।’ এই বলে চাকরটা তার হাফপেন্টের নিচে দিয়ে গরৈ মাছের মতো একটা জিনিস বের করে দিয়েছিল। রাহুল দেখেছিল চাকরটার হাতের মুঠোতে একটা বরফি ভাঙছে। মুখে দিলে গলে যাবার জন্য নির্মাণ হওয়া একটা বরফি!
কী আশ্চর্য শৈশব ছিল সেটা! মিষ্টি জিনিস খাওয়ার কী এক নেশা! কেবল মিষ্টি হলেই হল-চিনি, গুড়, লজেন্স এবং যেখানে যা।মিষ্টির জন্য লকলক করতে থাকা একধরনের লোভ থাকে শৈশবে। শালগ্রাম এবং ভগবানরা কেন এই লোভ দিয়েছিল রাহুলদের? সেই মিষ্টি জিনিস দেখিয়ে এই পৃথিবীতে কতজন কত শৈশবকে ফুসলিয়ে অন্ধকারের অরণ্যে নিয়ে গিয়েছিল।
একটি বন্য স্বপ্নের অন্ধ যাত্রা ( ২য় পর্ব) // নীলিম কুমার II অসমিয়া থেকে অনুবাদঃ বাসুদেব দাস