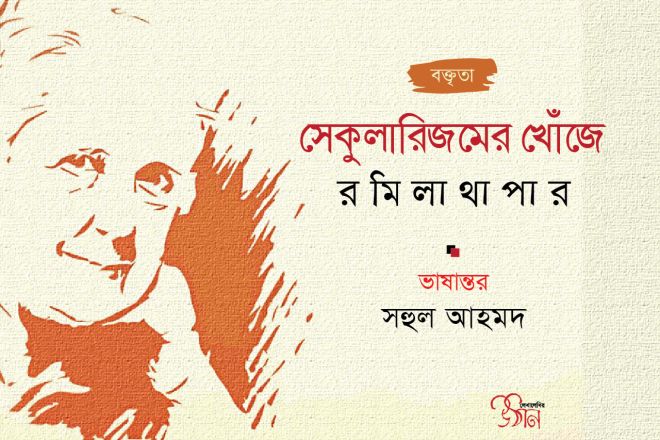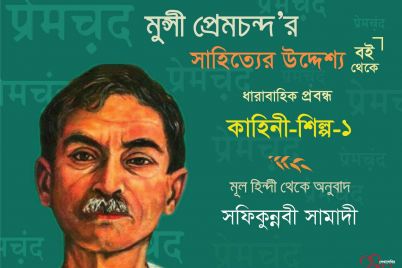[প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার লন্ডন ইউনিভার্সিটির, দিল্লি ইউনিভার্সিটি ও নয়া দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির প্রাচীন ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক; বর্তমানে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির এমিরেটারস অধ্যাপক। ২০১৫ সালের ১৯ আগস্টে রোমিলা থাপার জামিয়া মিল্লিয়াতে আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। পরবর্তীতে দ্যা ওয়ার (১৮ অক্টোবর ২০১৫) নামক ওয়েব পোর্টাল তার সেই বক্তৃতাটি What Secularism is and Where It Needs to Be Headed শিরোনামে প্রকাশ করে।]

ভারতীয় সমাজ ও সেকুলার বিষয়ক আলাপের শুরুতেই বলে রাখি, সেকুলারিজম নিছক রাজনীতি নয়, যদিওবা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এটাকে একটা রাজনৈতিক শ্লোগানে পর্যবসিত করেছে। ফলে, এক দল এটাকে তত্ত্ব হিসাবে সমর্থন করলেও এটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করে, আবার অন্যদল এটা নিয়ে মশকরা করে কেননা দলের মৌল মতাদর্শ হচ্ছে সেকুলার-বিরোধী। সেকুলারিজমকে সমর্থন করা বা খারিজ করে দেয়া কেবল রাজনৈতিক স্লোগান নয়; আমরা কী ধরণের সমাজ চাই – এই প্রশ্নের সাথে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ জন্যই বোধহয় স্বাধীনতার শুরুর বছরগুলোতে এটা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল, যেখানে বর্তমানে একে বাদ দেয়ার চেষ্টাই চলছে। সেকুলারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে ভারতীয় সমাজকে আমরা যেদিকে নিয়ে যাওয়ার নিয়ত করেছিলাম সেখানেই গুরুতর পরিবর্তন করা। সংবিধান থেকে যদি সেকুলারিজম বাদ দেয়া হয় তাহলে গণতন্ত্রই এর একটি শিকার হবে, আর অচিন্তনীয় ভবিষ্যতের কথা তো আছেই।
যদি আমরা সেকুলার সমাজ চাই, তাহলে আমাদের প্রধানত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, বা ভাষা দ্বারা নিজেদেরকে চিহ্নিতকরণ বন্ধ করতে হবে, এবং নিজেদেরকে একই ন্যশনের [যেহেতু নাগরিকের সাথে সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে সেহেতু ন্যাশনকে এখানে ‘রাষ্ট্র’ অর্থে পাঠ করাই শ্রেয়] সমান নাগরিক হিসাবে চিন্তা শুরু করতে হবে- তত্ত্বে ও চর্চায়। এর সাথে রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার এবং খোদ নাগরিকদের পারষ্পরিক বাধ্যবাধকতা জড়িত; সেটা কেবল হাল আমলের মতন তত্ত্বেই নয়, বাস্তবেও বটে। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, এবং অঞ্চলের মতো অন্যান্য পরিচয়গুলোর [আইডেন্টিটি] সম্পর্ক অনিবার্যভাবে গৌণ হয়ে উঠবে। এই পরিচয়গুলো এমনভাবে সমন্বয় করতে হবে যেন তা নিশ্চিত করে যে, তাদের নাগরিক অধিকারগুলোই সেখানে মুখ্য থাকবে। অবশেষে রাষ্ট্র কোনো ধরণের ধর্মীয় সংগঠনকে সমর্থন করবে বলে আশা করা হবে না, এমনকি বর্তমানে যাদের করা হচ্ছে তাদেরও করা হবে না।
আমি সেকুলার, সেকুলারিজম এবং সেকুলারকরণ [সেকুলারাইজেশন] বলতে কী বোঝাচ্ছি তা ব্যাখ্যার মাধ্যমেই আলাপ শুরু করতে চাই। সেকুলার হচ্ছে তাই যা দুনিয়াদারির সাথে সম্পর্কিত, এবং ধর্ম থেকে আলাদা। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্মীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণকে প্রশ্ন করাটা সেকুলারিজমের সাথে জড়িত। এটি এই বলে তার ন্যায্যতা আদায়ের চেষ্টা করে যে, সে নৈতিকতা [মোরালিটি] নিশ্চিত করে দেয়। কিন্তু সেকুলারিজমের মৌলিক যে নৈতিকতা সেটা কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং পুরো সমাজের কার্যকারিতা পর্যন্ত তা বিস্তৃত। সেকুলারিজম সমাজে ধর্মের উপস্থিতিকে খারিজ করে না, বরঞ্চ ধর্ম কোন কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর খরবরদারি করতে পারবে আর কোনটার উপর পারবে না তার সীমানা নির্দেশ করে দেয়। এই প্রভেদটা খুবই মৌলিক। এবং পরিশেষে সেকুলারকরণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তিত হয় এবং এই প্রভেদটাকে স্বীকার করে নেয়।
সেকুলারিজম কী এবং কী নয়
সেকুলার শব্দটি ১৮৫১ সালে যখন প্রথম ব্যবহৃত হয় তখন তার মাত্র একটিই মূল অর্থ ছিল। এটি সমাজের মঙ্গল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য মানবসমাজ সৃষ্ট নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত আইনসমূহকেই বোঝাত। এই আইনসমূহ যেমন খোদায়ী কর্তৃত্ব কর্তৃক প্রণীত হয়নি, তেমনি এর খোদায়ী কর্তৃত্বের কোনো অনুমোদনেরও প্রয়োজন পড়েনি। যারা এ সমাজ গঠন করেছিলেন তাদের ব্যাপকভাবে গৃহীত সহনশীলতা ও দায়বদ্ধতার মূল্যবোধের সাথে মিল রেখে সমাজের জন্য যা ভালো তা যুক্তি ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে তৈরি করে এই কর্তৃত্ব বজায় রাখা হতো। কর্তৃত্ব আইনের মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হতো। সামাজিক মূল্যবোধ তাই বেড়ে উঠতো যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা, তর্ক-বিতর্ক এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। [সমগ্র] সমাজ সম্মত নৈতিক বিধান (কোড) প্রতিষ্ঠার জন্য এর প্রয়োজন ছিল এবং এটি কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্ম, বর্ণ বা শ্রেণির সাথে সংযুক্ত ছিল না।
এর অর্থ হচ্ছে, যে আইন ও সামাজিক মূল্যবোধসমূহ সমাজকে পরিচালিত করে সেগুলোকে খোদায়ী আদেশ-নির্দেশ বহনকারী হিসাবে না দেখে সমাজের ভেতরকার আইন হিসাবেই পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ধর্ম-বর্ণ বা এমন যে কোনো কিছু থেকে পৃথক তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব রয়েছে। দেবতা এবং পরকালে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল ধর্মের অস্তিত্বও অব্যাহত ছিল। কিন্তু, নাগরিক (সিভিক) আইনগুলো সেকুলার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও পোষকতা লাভ করেছিল, এবং কোনো ধর্মের খোদায়ী অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে নি। তাই সেকুলারিজম বলতে আসলে ধর্মকে খারিজ করা বোঝায় না, বরঞ্চ সামাজিক কার্যক্রমের উপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের সঙ্কোচনকে বোঝায়। এবং আমি বারেবারে এই সংজ্ঞার প্রতি জোর দেব।

এই তত্ত্ব ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার পর এর বিভিন্ন প্রভাবও পড়েছিল। একটি হলো, পূর্বে যে সব বিষয়কে ধর্মীয়ভাবে সহি বলা হয়েছিল সেগুলোর বাইরে বের হয়ে জনগণকে চিন্তা করার স্বাধীনতা দিয়েছিল। আবার এর অর্থ ছিল না ধর্মকে ছুড়ে ফেলে দেয়া, বরঞ্চ এর অর্থ ছিল ধর্মীয় শেকল থেকে সামাজিক আচার-আচরণের বিধানকে মুক্ত করা। এটি মানুষকে অনৈতিক করে তুলে নি, যেমনটা অনেকেই তখন ভেবেছিলেন। কারণ আইন ভঙ্গের শাস্তির হুমকি কার্যকর করা হয়েছিল এবং এই ইহজীবনেই অবিলম্বে শাস্তিও পেতে হয়েছিল। অধিকাংশ ধর্মীয় বিধানের মতো শাস্তিকে আখিরাতের জন্য রেখে দেয়া হয়নি। সুতরাং এটি মানুষকে তাদের আইনকানুনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল, এবং এই চিন্তাটা সর্বদা খুবই দরকারি। লোকে যখন আইনের উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারে তখন সেটি মান্য করাও জোরদার হয়।
কোনো বিষয়ের সম্ভাব্য সমাধান খোঁজার অর্থ হলো মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা শেখা। চিন্তা করাটা আসে তাদের শিক্ষা থেকে। ফলে সবকিছুই খোদায়ী পরিকল্পনার অংশ বা সবকিছুর জন্য খোদায়ী বিধানের প্রয়োজন এমন ব্যাখ্যা সবসময় সাধারণ সহজ সরল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিল না। অতএব শিক্ষা ধর্ম ও বিশ্বাস ভিত্তিক ব্যাখ্যার বাইরে বিভিন্ন ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে, এমনকি প্রয়োজন অনুসারে এই ব্যাখ্যাগুলোকেও ঘষামাজা করে নিচ্ছিল। কিন্তু আমরা যে প্রাকৃতিক ও মানব জগতে বসবাস করি সেটার যৌক্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সামাজিক আইনগুলো জন্ম নিতে শুরু করে। মাঝে মাঝে কল্পনার সামান্য কোনো স্ফুরণও (ইমাজিনেটিভ লিপ) এমনকি শেষপর্যন্ত যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে, আইনসমূহের ব্যাখ্যা এবং এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা শিক্ষার একটা জরুরি অনুষঙ্গে পরিণত হয়, এবং একইভাবে সেকুলার হয়ে উঠার নিহিত্যার্থ বিষয়ক চিন্তাভাবনার অংশে পরিণত হয়।
ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল ব্যক্তির ভাবগত প্রয়োজন হিসাবে। এটি এরপর বিস্তৃত হয়েছে ব্যক্তি কীভাবে জীবনের অভিজ্ঞতা নিচ্ছে এবং এর বাইরে এই মহাজগত কীভাবে কাজ করছে পর্যন্ত। এই সবকিছুই অতিপ্রাকৃত কোনো এক শক্তির কাছে আরোপ করা হয়েছিল যিনি ছিলেন পূজনীয়। ধীরে ধীরে এই ব্যক্তিগত [পারসোনালাইজড] ধর্ম একটি জটিল সংগঠিত ধর্মে রূপান্তরিত হয় এবং সমাজ ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের উচ্চাভিলাষী প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। এই পরিবর্তনের মাধ্যম ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠে, তেমনি কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণেও শক্তিশালী হয়ে উঠে। কোনো কোনো স্থানে এর ক্ষমতা রাষ্ট্রের ক্ষমতার সাথে সমান্তরাল ছিল। ধর্মের এই বিশেষ দিকটি, মানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ধর্মীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণের দিকটি একজন সেকুলার ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে রাখতে চান। এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা প্রায়শই এটা উপেক্ষা করি, এবং দাবি করি যে সেকুলারিজম ধর্মকে পুরোপুরি অস্বীকার করে।
সেকুলারিজম তখন আরো একটি অর্থ ধারণ করে। মানুষের এই আইনগুলো তৈরি ও পালনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ধর্ম থেকে আলাদা হওয়া উচিত, কেননা ধর্মের অনুমোদন আসে বিশ্বাস ও দেবতা থকে। প্রত্যেকের কর্তৃত্ব স্পষ্টতই পৃথক ছিল।
সামাজিক আইনগুলো হচ্ছে একটি সমাজের মেরুদণ্ড। আইনগুলোর উচিৎ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে রক্ষা করা, এবং জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করবে এমন কোনো বৈষম্য যেন না ঘটে সেটা নিশ্চিত করা। এটা মানুষের জীবনচক্রের বিভিন্ন বাকবদলকে রক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ; জন্ম, বিবাহ বা বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন করা, সমাজে সামাজিক হয়ে উঠার জন্য শিশুর জন্য শিক্ষার প্রক্রিয়া, পেশা ও কর্মসংস্থান, এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ইত্যাদির জন্য আইনগুলো দরকারি। এসবের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো নাগরিক আইনের আওতার মধ্যে পড়ে। এই সম্পর্কটাকে কার্যকর করে তোলার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রে সামাজিক আইনগুলোকে অবশ্যই কল্যাণমূলক কিছু প্রাথমিক বিষয় সরবরাহ করতে হবে। যেমন এর মধ্যে ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিক আইনগুলো যদি সর্বজনীন এবং অভিন্ন হয়, যেমনটা সেকুলার সমাজে হওয়া দরকার, তাহলে রাষ্ট্র কর্তৃক অবশ্যই এর নিশ্চয়তা দিতে হবে। কোনো ভাবেই কোনো ধরণের বৈষম্য পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য।
সুতরাং সেকুলার সমাজেও ধর্মীয় কর্তৃত্ব বহাল থাকে, কিন্তু সীমিত আকারে। এটা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার পর্যন্ত বিস্তৃত। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো কঠিন দেয়াল থাকা উচিত নয়, কিন্তু দুটোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক নিয়মমাফিক দূরত্ব থাকতে পারে। এটি ধর্মের ভেতরে অথবা ধর্মগুলোর মধ্যে অথবা ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে নতুন ধরণের বিন্যাস সম্ভব করে তুলতে পারে। এই সামগ্রিক সম্পর্ক এক ধর্মের উপর আরেক ধর্মের আধিপত্যকে খারিজ করে দেয়, কারণ রাষ্ট্রে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে, এবং আইনের সামনে সকলেই সমান। তথাপি এই বিন্যাসের মধ্যে একটা মাত্রা পর্যন্ত নির্ধারিত দূরত্ব থাকে যেন ধর্মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সামাজিক আইনকানুনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে।
‘ভারতীয়’ সেকুলারিজম
মাঝেমধ্যে সেকুলারিজমের যে ভারতীয় সংজ্ঞা প্রদান করা হয়, মানে সকল ধর্মের সহাবস্থান, এটা এবং সেকুলারিজম অবশ্যই এক জিনিস নয়। নিছক সহাবস্থান অপর্যাপ্ত, কেননা এখানেও ধর্মগুলো অসম হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, এবং কিছু ধর্মকে প্রান্তিক করা হতে পারে, যেমনটি প্রায়শই করা হয়ে থাকে। আইনের সামনে সকলের সমান মর্যাদার সাথে সহাবস্থানের স্বীকৃতি অবশ্যই প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে হবে। কিন্তু, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে, এটি কতদূর যাবে এবং এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত।
ধর্মগুলোর সহাবস্থানের ভিত্তিতে এই সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ, কেননা এখানে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের আইনগত অধিকারের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়নি। কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে দেয়াল তুলে দেয়াটা নিয়ত হতে পারে না। নিয়ত হতে হবে কোন কোন কাজ নাগরিক (সিভিল) আইনের অধীনে আসবে এবং কোন কোন কাজ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সংগঠন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে তার সীমানা নির্দেশ করা। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমতা বা ইকুয়ালিটি অপরিহার্য, যেমন করে অপরিহার্য এটা ব্যাখ্যা করা যে কে কোন আইন নিয়ন্ত্রণ করবে। সমসাময়িক ভারতে, ধর্মের সহাবস্থান বিদ্যমান, তবে তাদের সমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেকুলার একটু কম প্রতীয়মান, এমনকি কেউ কেউ বলতে পারেন কার্যত অনুপস্থিত। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সবসময় ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে নিজেকে দূরে রাখে না। প্রকৃতপক্ষে, কখনো কখনো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখে।
কেউ কেউ সেকুলারিজমের বিরোধিতা করে এই যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, এটি পশ্চিমা ধারণা এবং ভারতের জন্য উপযুক্ত নয়। জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বেলাতেও একই কথা বলা উচিত না? উভয়ই স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের জন্য নতুন। এবং অবশ্যই নতুন মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে আমাদের আত্তীকরণ করা তো পশ্চিমা ছাপের চাইতেও শক্তিশালী। সমাজের সেকুলারকরণকে সমর্থন করার মানে নিজেকে কোনো একটা পশ্চিমা ধারণার অধীনস্থ করা নয়, বরং আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করা। জাতি-রাষ্ট্র হওয়া তো একেবারেই আধুনিক জমানার অভিজ্ঞতা, এবং হাল আমলের পুরো দুনিয়াতেই এটি বিদ্যমান। আমাদের কাছে নতুন হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রকে আমরা সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে বেছে নিয়েছি। আমি বলি যে, গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য সেকুলার সমাজ অপরিহার্য।

এখন আমি নির্দিষ্টভাবে এই বিষয়ের ভারতীয় দিকের প্রতি নজর দিতে চাই, এবং এটি আমাদের সময়ে কীভাবে দেখা হচ্ছে তার সাথে তুলনা করার জন্য আমি অতীতে ধর্ম এবং সমাজকে কীভাবে দেখছি তা নিয়ে বলতে চাই। আমার যুক্তি হচ্ছে যে, আমরা কীভাবে নিজেদেরকে দেখছি এই বিষয়ে উপনিবেশায়ন একটা গুরুতর বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, এবং আমরা তা খুব একটা প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিয়েছি। যে কোনো ধরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সামাজিক পরিবর্তন, বড়সড় পরিণামসহ, সামলানো একটু সহজ হয় যদি সমাজের পূর্বেকার ঐতিহাসিক রূপ এবং এর ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের দিকে নজর দেয়া যায়। যাই হোক না কেন, বর্তমান তো অতীত থেকেই উৎসারিত। সমাজ ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, ভারতে কীভাবে ধর্মগুলো কাজ করেছিল এই বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা আমরা লালন করে চলছি। এই ধারণাগুলো এসেছে ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যেগুলো আমরা পর্যাপ্ত প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করে নিয়েছি। সুতরাং এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দরকার হতে পারে।
ধর্মের উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি
উপনিবেশিক ধারণাগুলোর ভিত্তি ছিল ইউরোপিয়ান সমাজের প্রেক্ষাপটে ধর্ম বিষয়ক ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা। ইউরোপের প্রসঙ্গে চার্চ এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণকে প্রায়শই সেকুলারিজম হিসেবে বর্ণনা করা হয়। একে একমাত্রিক সম্পর্ক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কারণ সাধারণত সেখানে ধর্মটি ছিল একটি মনোলিথিক ধর্ম। এটা এতো জোরালোরূপে জাহির করা হতো যে, ইউরোপে যারাই ক্যাথলিক বিশ্বাস ও আচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেন তারা ধর্মদ্রোহী হিসেবে কঠিন শাস্তির মুখে পড়তেন। কাউকে পোড়ানো হয়েছিল, গ্যালিলিওর মত কাউকে মতামত ত্যাগ করতে হয়েছিল, এবং আরো নানান শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যদিও প্রটেস্টান্টদের মতবাদ ও আচরণ পরবর্তীতে অনেক নমনীয় হয়েছিল, তবে পূর্বের অভিজ্ঞতা কেউ ভুলেনি।
উপনিবেশকদের কাছে ধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই পরিচিত ছিল। এই চোখ দিয়ে তারা ভারতীয় ধর্মকে পাঠ করেছে। ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক পাঠ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই দৃষ্টিভঙ্গিটা ত্রুটিযুক্ত ছিল, সুতরাং একে পুনরায় তলিয়ে দেখা দরকার। ভারতীয় সমাজের উপনিবেশিক দৃষ্টি হিন্দু ও মুসলমান এই দুটো জাতির খোঁজ পেয়েছিল, যে দুটোই মনোলিথিক ধর্মীয় পরিচয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং অন্তর্নিহিতভাবে একে অপরের সাথে বৈরীভাবাপন্ন। এবং তাদের পারষ্পরিক এই শত্রুতার কারণেই একটি বহিরাগত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জরুরত ছিল। এটাই উপনিবেশিক শাসনের জায়েজিকরণের একটি যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক ইতিহাসবিদ যেমন উল্লেখ করছেন, এই ছবিটা ভারতীয় ইতিহাসের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া, বিশেষত মধ্যযুগের ইতিহাসের উপর। এ জোরারোপ দুই ধর্মের মধ্যে দূরত্ব স্থাপনে বাধ্য করেছিল।
ধর্ম কর্তৃক চিহ্নিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধারণাটিও উপনিবেশিক নীতি দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। এটি মনোলিথিক ধর্মের ধারণাকে আরো সুসংহত করেছিল, এবং এটাই পরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে জ্বালানি জোগায়। স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘুর সম্প্রদায় অবশ্য গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী। যখনই বিপুল সংখ্যাক লোক কোনো একটি নির্দিষ্ট মতামতের সমর্থনে জড়ো হয়, তখন প্রতিবারই গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি হয়। সংখ্যাটি অন্য যে কোনও গ্রুপের চাইতে বেশি হতে হবে, এবং অন্য গ্রুপের সাথে পূর্ববর্তী সম্পৃক্ততা এই নতুন গ্রুপে যোগদানে বাধা দিবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার গঠন তাই কোনোভাবে কোন প্রাক-বিদ্যমান ধর্মীয়, বর্ণ ও ভাষিক পরিচয়ের ভিত্তিতে হয় না। প্রতিটি ইস্যুর সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের উপাদানগুলো পরিবর্তিত হয়। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো স্থায়ী সদস্য নেই।
উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ এই ছবিকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন, কেননা বিস্তৃত জাতীয়তাবাদকে অবশ্যই ইনক্লুসিভ হতে হবে, বিভিন্ন ধারার মতামতকে জায়গা দিতে হবে, এবং অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাসের কাছে যেতে হবে। এই অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাসটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি এরিক হবসমকে উদ্ধৃত করে চাই, তিনি লিখেছিলেন যে, আফিমখোরের জীবনে আফিম যে ভূমিকা পালন করে, জাতীয়তাবাদের ইতিহাসও সেই ভূমিকা পালন করে। এটাই উৎস। এটাই পরিচয়ের ধারণাকে পুষে। উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এই মনোলিথিক ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেনি। এদের বৈরিতা অস্বীকার ও সহাবস্থানকে তুলে ধরার দিকেই নজর দিয়েছিল। এটাই সেকুলারিজম ধারণার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এটি পুরোপুরি সফল হয় নি। একটা কারণ হচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান জাতীয়তাবাদ, যা কিনা ভারতের সাম্প্রদায়িক জমিন তৈরি করেছিল, তার মৌলিক মতাদর্শিক ভিত্তি হচ্ছে ভারতের ধর্মের উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি আগেও ছিল এবং এখনও আছে। অন্যভাবে বললে, উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ এবং দুই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, দুটোর ভিত্তি হচ্ছে ভারতীয় ধর্মের উপনিবেশিক নির্মাণ, যদিও প্রথমটা একটু কম ধার করেছে, এবং পরেরটা একেই তাদের মতাদর্শিক ভিত্তি বানিয়ে তোলে। প্রায় একশ বছর বা তারও পূর্বে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিল। এগুলো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না, বরঞ্চ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহারের মতাদর্শ ছিল। বর্তমানে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দু, মুসলিম, শিখসহ অন্যান্য অনেক ধর্মীয় সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করে, যারা রাজনৈতিকভাবে উচ্চাভিলাষী ও উদ্বিগ্ন, এবং নিজেদের রাজনৈতিক ভোট নিশ্চিত করতে সম্প্রদায়ের আইন-কানুনের উপর তাদের খবরদারি অব্যাহত রাখতে চায়। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে ইতিহাস অংশীদারিত্বমূলক নয়, এটা বিভেদজনক এবং রণভূমিতে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের নিয়ে লড়াইটা তাই কোনো এক নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি ইতিহাসের পক্ষপাতিত্ব দেখানোর প্রয়াস এবং অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাসকে অস্বীকার করার চেষ্টা।
আমরা তাই জিজ্ঞেস করতেই পারি, পূর্ব থেকে ভারতীয় সমাজে ধর্ম এভাবেই কী সক্রিয় ছিল? আমরা কি অতীতকে বিশ্লেষণ করেছি? আমরা কি অতীতে ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি? এই সংগঠনগুলো কোন রূপ নিয়েছিল, কীভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিল এবং সমাজের কোন অংশ কোন সংগঠনকে সমর্থন দিত?
ভারতীয় ইতিহাসে ধর্মের অবস্থান
আমার যুক্তি হচ্ছে, ভারতের ধর্মের ঐতিহাসিক ছবিটা জটিল ছিল। এটা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের একটি সহজ বাইনারি ছিল না, কারণ ধর্মগুলো কোনো এক বৃহৎ মনোলিথিক সম্প্রদায়ের ছিল না, বরং প্রতিটি ধর্মের আবার বিভিন্ন উপদলের [‘sect’ এর অনুবাদ এখানে উপদল করা হয়েছে। কেউ কেউ উপাসক সম্প্রদায়ও অনুবাদ করে থাকেন] সুবিন্যস্ত রূপ ছিল। আমি দুই ধরণের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এটা দেখি, প্রত্যেকটিরই ধর্ম ও সমাজের মধ্যকার যোগসূত্র অনুসন্ধানের প্রয়োজন। প্রথমটি ছিল ভারতীয় সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান কাস্ট বা জাতসম্বন্ধের মাধ্যমে একটা ঘনিষ্ঠ সামাজিক যোগসূত্রতার সাথে উপদলের মিথস্ক্রিয়া। দ্বিতীয়টি ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সাথে ও মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা, যা উপদল, জাতিপ্রথা [কাস্ট] এবং রাষ্ট্র মিলে একটি ত্রিমুখী প্রক্রিয়াতে পরিণত হয়েছিল। সবগুলো উপদলকে একত্রে কোনো একটি একক সত্ত্বায় নিয়ে আসার জন্য এখানে কোনো চার্চ ছিল না। অন্য ভাবে বললে, আমি ধর্মের দিকে আরো বেশি বিকেন্দ্রীভূত নজর দেয়ার কথা বলছি।
ভারতীয় অতীতে একাধিক ধর্মীয় উপদল এবং বহু জাতের [কাস্ট] মধ্যকার সংযোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। উপদল বিশ্বাস প্রচার করতো, জাত এর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারণ করে দিত। দুটোর আন্তঃনির্ভরতার মাধ্যমে মর্যাদা পরিমাপ করা হত। ধর্মের উঁচু জাতেরা – তা জাতের অনুশাসন কঠোরভাবে পালন করুক আর নাই করুক- তারা ধর্মের গ্রন্থ-নির্ভর আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। অন্য দিকে নিচু জাতেরা, তারা কম গ্রন্থ-নির্ভর হওয়াতে, অনেক বেশি নমনীয় ছিল। জাত সামাজিক বিধান [কোড] নির্ধারণ করে দিত, যারা শিক্ষিত ও আইন জানতেন বলে দাবি করতেন তারাই এটা আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কিন্তু অধিকাংশের কাছে এটা ছিল ঐতিহ্যের জনশ্রুতি। সামাজিক বিধানের উপর জাত ও উপদলের কর্তৃত্বকে এখন সবার জন্য প্রযোজ্য নাগরিক [সিভিল] আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। এর জন্য নাগরিক আইনের সেকুলারিটি এবং এর সামাজিক ন্যায়বিচারের অনুমোদনকে নিশ্চিত করতে সকল ধর্ম স্বীকৃত নাগরিক আইনের দিকে নতুন করে তাকানোর দরকার হবে। সেকুলারিটি এবং সামাজিক ন্যায় বিচার মূল্যবোধ হিসেবে পরিচিত হলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগ নতুন।
ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর উপর বিভিন্ন মূল্যবান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা করা হয়েছে যা এগুলো সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াকে আরো সমৃদ্ধ করছে। তবু বিশ্বাস প্রচার করতে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এজেন্সি হিসেবে বিভিন্ন ধর্ম যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলেছে সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে একটু কম মনোযোগ দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে মনোলিথিক অবিচ্ছিন্ন একটি ধর্মীয় সমাজের দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে আমরা যদি ধর্ম ও সমাজের পারষ্পরিক সম্পর্ককে বোঝার জন্য জাত ও উপদলের সম্পর্ককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি তাহলে সেটা আরো বেশি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ হবে। জাত ও উপদলের মধ্যকার সম্পর্কে এক ধরণের নমনীয়তা ছিল, এমনকি তরলতাও ছিল যা মনোলিথিক ধর্মে অনুপস্থিত। এরপর আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি অনড়তা [রিজিডিটি] ধর্মের মধ্যে কম এবং বর্ণবৈষম্যের [কাস্ট ডিসক্রিমিনেশন] মধ্যে বেশি ছিল কি না। এই ক্ষেত্রে, ভারতে ধর্মের উপনিবেশিক নির্মাণ যা খুব সহজেই আমরা গ্রহণ করেছিলাম, তাকে আবারো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সম্ভবত আমাদেরকে সতর্কভাবে দেখতে হবে, কীভাবে অতীতে জাত, এবং বর্তমানে তার পরিবর্তে শ্রেণি, ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ককে রূপ দিয়েছিল এবং দিচ্ছে। সমাজের কোন গোষ্ঠী কোন রাজনৈতিক-ধর্মীয় সংগঠনকে সমর্থন দেয় এবং কেন দিয়ে থাকে?
প্রাক-ইসলামি যুগে, হিন্দুধর্মের কোনো মনোলিথিক ধরণ এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। মজার বিষয় হচ্ছে, আমরা বর্তমানে যেভাবে ‘হিন্দুইজম’ ও ‘বুদ্ধিজমে’র ব্যবহার করি, তেমন লেবেল হিসেবে ধর্মকে উল্লেখ করা হতো না। পরিবর্তে সেখানে দুই ধরণের বিস্তৃত বর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা স্বতন্ত্র ধারণা প্রচার করেছিল। এগুলো ছিল ব্রাহ্মণ (Brahmana) ও শ্রমণ (Shramana)। মূল পার্থক্যের ভিত্তি ছিল ঐশ্বরিক এবং পরজন্মের তত্ত্বগুলোর উপর বিশ্বাস করা বা খারিজ করা। ব্রাহ্মণ বলতে বোঝাতো ব্রাহ্মণবাদী বিশ্বাস ও আচার, এবং শ্রমণ বলতে বোঝাতো বৌদ্ধ, জৈন, অন্যান্য প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ অবস্থানকারীরা, নাস্তিক/অবিশ্বাসী, এবং তাদের অনুসারীগণকে। এরা বেদ, মানে ঐশ্বরিক বিধিবিধান ও আত্মার ধারণাকে অস্বীকার করতেন। ফলে তারা জগত ও মানব জীবনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই দুটোর মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাসের স্বতন্ত্র উপদলগুলোও স্বীকৃত হয়েছিল।
এদের কোনোটাই মনোলিথিক গোষ্ঠী ছিল না, এরা ছিল বিচিত্র উপদলের সমাহার। আমরা যেগুলোকে আজ ধর্ম বলি সেগুলোর সাথে জড়িত বিভিন্ন গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের এই দ্বৈততা এখনো ব্যবহৃত হয়; সম্রাট অশোকের নির্দেশনামা প্রচার থেকে শুরু করে মেগাস্থিনিসের বিবরণী, চীনাদের সফর এবং ১১ শতকের আলবিরুনী পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ বছর ধরেই এটা ছিল। বিষ্ণু পুরানের মতন ব্রাহ্মণীয় পাঠে এবং বৌদ্ধিক পাঠেও দুই গোষ্ঠীর মধ্যকার বৈরীভাবের কথাও উল্লেখ রয়েছে। মজার বিষয় দু গোষ্ঠীই একই ধরণের অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করতো। ব্যাকরণবিদ পতঞ্জলি দুই গোষ্ঠীর কথাই উল্লেখ করেছেন এবং এদের মধ্যকার সাপে-নেউলে সম্পর্কের কথাও যুক্ত করেছেন।
তৃতীয় যে বর্গটার কথা উল্লেখ করা হয় নি, সেটা হচ্ছে যারা জাতের কারণে বা জাত না থাকার কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। এ কারণে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ব্যবস্থা ও উপাসনার ধরণ ছিল। এই বর্গ জাত প্রথার মধ্যেই নিহিত ছিল। আমরা যাদেরকে দলিত বলি তাদের সমতুল্য প্রতিটি ধর্মেই বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়, যেমন পাজমান্দা, মাজহাবি ইত্যাদি। এমনকি যে ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশ্বাস করে খোদার চোখে সবাই সমান, তাদের মধ্যেও দলিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নির্বিশেষে সকল দলিতেরই সমান অধিকার থাকা উচিত, তবে এটি সাধারণত মানা হয় না।
বিভিন্ন উপদলের গুরুত্ব
সময়ের সাথে সাথে যে একাধিক উপদলের আবির্ভাব ঘটে, এর কয়েকটি সনাতনী সমর্থক ছিল এবং কয়েকটি প্রচলিত মতের বিরোধী ছিল। মনোলিথিক ধর্মের উপর উপদলের সুবিধা হলো এই যে, বেশি গোঁড়া থেকে শুরু করে কম গোঁড়া পর্যন্ত সকলের উপর একটা ছায়া ফেলে। এটি কম গোঁড়াদের নতুন নতুন বিশ্বাসকে একীভূত করার অনুমোদন দেয় এবং এগুলোকে ধর্ম-বিরুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ধর্মদ্রোহীরা নিজস্ব ধারায় কাজ করেন।
ধর্মান্তর সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া আরো পরিষ্কার হবে যদি আমরা উপদল ও জাতের দিকে মনোনিবেশ করি; যতদূর পর্যন্ত ফিরে যাওয়া যায় বা প্রমাণাদি পাওয়া যায়। হিন্দুরা মুসলমান হয়ে গিয়েছেন- কেবল তা উল্লেখ না করে বরঞ্চ এটি আরো অনেক ভালো ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবে। অতীতের ঐতিহাসিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত আমাদের বোঝাপড়া হাল আমলের মিথস্ক্রিয়া বিষয়ক চিন্তাভাবনাকে আরো স্পষ্ট ছাঁচ দিতে পারে। ফলে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আরো বেশি বিশ্লেষণাত্মক হওয়া আমাদের দায়িত্ব। ইতিহাসকে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক শ্লোগানে পর্যবসিত করা উচিৎ নয়।
যে কোনো উপদলের সৃষ্টি উন্মুক্ত ছিল, এবং এটি এমন এক বহুত্বের দিকে নিয়ে যায় যা ভারতের প্রতিটি ধর্মের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এটি ধর্ম ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ককে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক গঠন করে। এই সম্পর্কগুলো সমাজভেদে ভিন্ন হয়। আমরা তাই ধরে নিতে পারি না যে, ইউরোপের জন্য ধর্মের যে ভূমিকা দেখা গিয়েছিল, সেটা ভারতেও হুবহু প্রয়োগ করা যাবে। এটি উপনিবেশিক বুদ্ধিবৃত্তিক গলদ ছিল। এর অর্থ এই না যে, সেকুলারিজমের অর্থ বদলাতে পারে, বরং একটি সমাজে এটি যেভাবে প্রবর্তিত হয়েছে সেটা ভিন্ন হতে পারে।
যেহেতু শ্রমণবাদ [Shramanism] মূলত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতাদের উপর ভিত্তি করে ছিল, এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভিন্ন শাখার সাথে মোটামুটি রৈখিক রূপ নেয়। ব্রাহ্মণবাদের [Brahmanism] ইতিহাস আরো অনেক জটিল। প্রাথমিক পর্যায় ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণবাদ, বিভিন্ন দেবতা বিশেষত ইন্দ্র ও অগ্নির নামে যজ্ঞকে প্রাধান্য দেয়া হতো, এবং উঁচু জাতের হিন্দু কর্তৃক এটি সম্পাদিত হতো। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, জৈন এবং অজিভিকদের মতো বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত মত বিরোধী সম্প্রদায় এই বিশ্বাসগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলে। এই সম্প্রদায়গুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করতো, এবং গোঁড়ামিকে প্রশ্ন করার পর্যালোচনামূলক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, যদিও শেষপর্যন্ত তারাও তাদের গোঁড়ামি প্রতিষ্ঠা করেছেন।
খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা ব্রাহ্মণ রীতিকে আরো বিশিষ্ট চরিত্র দান করে। উপাসক উপদলগুলো বিশেষ বিশেষ দেবতাদের দ্বারা চিহ্নিত হতেন, যেমন বৈষ্ণব ভগবৎ এবং শিবা পাশুপথা। সপ্তম শতাব্দী থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনা ভক্তিমূলক সম্প্রদায়ের [সেক্ট] রূপ ধারণ করে, যাদেরকে আমরা ভক্তি সম্প্রদায় বলি। তারা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে উত্থিত হয়েছিলেন। প্রথমদিককার স্বীকৃত কয়েকটি হচ্ছে দক্ষিণের আলভার ও নয়ন্যার, এবং উত্তরে এদেরকে অনেকে অনুসরণ করেন। এদের পরবর্তী অনেকের মধ্যেই নতুন নতুন ধর্মীয় ধারণা প্রতিফলিত হয়েছিল।
ব্রাহ্মণবাদ ও শ্রমনণবাদ উভয়ই প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, এবং সম্পদশালী, শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত ধর্মে পরিণত হয়েছিল। এগুলো তাদেরকে মর্যাদা এনে দিয়ছিল এবং সামাজিক আইনকানুন নিয়ন্ত্রণে সক্ষম করে তুলেছিল। তখন অনুদান দেয়া হতো বিভিন্ন উপদলকে, কোনো মনোলিথিক ধর্মীয় সত্তাকে নয়, কারণ এর অস্তিত্বই তখন ছিল না। পরবর্তী সময়েও এটি নিয়ম হিসেবে চালু ছিল।
সম্পদশালী উপদলের কেন্দ্রগুলো শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এটি তাদের কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত হয়েছিল এবং তারা অভিজাতদের অভিষিক্ত করাতে পারতো। প্রায়শই, বৃহৎ অনুসারীদল এবং কর্তৃত্বসহ উপদলগুলো নিজেদের মধ্যে জাত হিসেবে কাজ করা শুরু করে দিতে পারতো, যেমন কর্ণাটকের লিঙ্গায়েত, এবং দেশের বিভিন্ন অংশে এমন অনেকেই। তারা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাথে চিহ্নিত নাও হতে পারতো, এবং কেউ কেউ আসলে এর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতাও করেছে। কিন্তু উপনিবেশিক নথিতে এদের সবাইকে বাইনারি বর্গের যে কোনো একটায় ফেলে দেয়া হয়েছিল।
ইসলামের আগমন
ইসলামের আগমনের সাথে সুফিদের উপস্থিতির ফলস্বরূপ এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় ধারণার (অর্থোডক্স এবং হেটারোডক্স) সম্প্রসারণ ঘটেছিল, যেমন করে বেড়েছিল উপদলের সংখ্যাও। কোনো কোনো উপদল একেবারে গোঁড়া অবস্থান গ্রহণ করেছিল, কেউ কেউ মিশ্রিত বিশ্বাস ও উপাসনার পথ বেছে নিয়েছিল। এই পরের উপদলগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল।
এই নতুনের উপস্থিতি চিহ্নিত করা হয়েছিল রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক ও বিত্তবান কর্তৃক নির্মিত মসজিদ ও খানকার বিস্তৃতির মাধ্যমে। ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পদশালী হয়ে উঠছিল, যেমন করে সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ধর্মের বেলায় ঘটেছে। বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু মন্দির ও মঠগুলোর মতো ইসলামি কেন্দ্রের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের অনুসারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক জগতে অংশ নিতে সক্ষম করে তুলেছিল। আমাদের যেগুলোকে হিন্দু, মুসলিম, শিখ বলি তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিস্তর অধ্যয়ন আমাদের জন্য সহায়ক হবে।
আগের যুগের মত উপদল ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ধর্মীয় পরিচয়। এটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা ইসলাম আগমনের সাথে জড়িত দুটো প্রক্রিয়ার কথা বলি: বসতিস্থাপন এবং ধর্মান্তর। বর্তমানে এই ঘটনাকে আগ্রাসন ও এর রাজনৈতিক পরিণতির দিক থেকে আলাপ করা হয়, এবং এটাই জনপ্রিয়। কিন্তু এর আরো অনেকগুলো উপায় ছিল যেমন, ব্যবসায়ী, অভিবাসী, সুফি ও এমন আরো অনেকের বসতিস্থাপন।

মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে আমরা জানি। কিন্তু এর চাইতে বেশি কৌতূহলীদ্দোপক বিষয় হলো সিন্ধু থেকে কেরালা পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব ব্যবসায়ীদের বসতিস্থাপন। কিছু কিছু আরব অষ্টম এবং নবম শতকের দিকে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজাদের চাকরিতে যোগ দেন। এই উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অত্র অঞ্চলে রীতি অনুযায়ী মন্দির ও ব্রাহ্মণদেরকে জমি অনুদান করার অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। আরব বণিকরা স্থানীয়দের বিয়েশাদি করে, এবং বিদ্যমান ধর্মগুলোকে ধারণ করে নতুন নতুন সম্প্রদায় নতুনভাবে বিকশিত হচ্ছিল। অনিবার্যভাবে এইগুলো নতুন উপদলে পরিণত হয়েছিল – যেমন বোহরা, নবায়তের খোজা, মাপ্পালিয়সহ এমন অনেক। তারা তাদের বিশ্বাস, আচার এবং নাগরিক আইনকানুন বিদ্যমান প্রথা থেকে গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা করেনি। ফলে কোনো দুটোই অভিন্ন ছিল না। গুজরাতের বোহরাদের সাথে মালায়লি মাপ্পালিয়াদের সম্পর্ক অল্পই ছিল। এমন বহু উপদল সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু সমাজ ও ধর্মের ইতিহাসের অংশ হিসেবে এগুলো নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা করা হয়নি।
এমন রীতি বা প্যাটার্ন সমাজের ব্যাপক স্তরে পরবর্তীতে শতকেও অব্যাহত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসন থেকে উদ্ভূত অন্যান্য রীতির উত্থান সত্ত্বেও এটি বজায় ছিল। এমন দ্বিবিভাগগুলো [dichotomies] ইতিহাসজুড়েই ছিল, এবং কেবল তাদের উপাদানগুলো পরিবর্তিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মমতের নতুন উদীয়মান শিক্ষকরা সহায়ক অনুগামীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। উপনিবেশিক যুগে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোকে অনুসরণ করার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ভারতীয় কীভাবে ধর্মের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এই প্রশ্নে এখন পর্যন্ত এগুলোই মূলসূত্র হিসেবে রয়ে গিয়েছে। হিন্দুত্ব ও ইসলামিকরণ প্রবেশের পূর্বে এটাই ছিল; এগুলো এখন সীমানাকে কঠিন করে তুলেছে এবং এমনকি চর্চাও পরিবর্তন করে ফেলেছে। এই সময়ের অনেকেই যারা কোনো একটি মনোলিথিক ধর্মের নামে নিজেকে চিহ্নিত করেন, তাদেরকে একটু চাপ দিলেই দেখা যাবে তিনি কোন সম্প্রদায় বা কোন বাবা বা গুরু বা পীরের অনুসারী সেটা উল্লেখ করছেন। তাদের জীবনযাপনের সাথে এই সংযোগ অনেকবেশি প্রাসঙ্গিক বা সম্পর্কযুক্ত। এবং মজার বিষয় হলো, তারা যে উপদলগুলোর নামে নিজেদের পরিচয় দেন সে সম্প্রদায়গুলো বিগত হাজার বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে মিথ-নির্মাণ
ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ, যাকে উপনিবেশিক ইতিহাসবিদরা মুসলিম আমল বলে অভিহিত করেন, সেটা গত একহাজার বছরেই অবস্থান করে। এই ইতিহাস সম্পর্কে ধর্মীয় উগ্রবাদী ও রাজনৈতিক নেতারা যে শ্লোগান দেন, ‘আমরা দাস ছিলাম’, সেটা আসলে এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে, ইসলামি স্বৈরশাসন হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর জুলুম করেছিল। এটা আসলে ভারতের ইতিহাসের উপনিবেশিক পাঠের ধারাবাহিকতা, যা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে এই দৃশ্যের সাথে বিভিন্ন স্তরে প্রচুর ফারাক দেখা যায়।
আমরা যাকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম বলি তাদের পারষ্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় পরপষ্পরবিরোধী রাজনীতির সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত ছিল। এটি প্রায়শই ধর্মীয় সংগঠনসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালে যে বিষয়টা বহুলাংশে রাজনৈতিক কর্ম ছিল সেটা বর্তমানে [রাজনীতিকে বাদ দিয়ে] নিখাদ ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কিছু কিছু সংঘর্ষ প্রত্যাশিত ছিল। এই ধরনের সংঘর্ষ ভারতে নতুন কিছু ছিল না। পূর্বে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের মধ্যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক ছিল। এটাই বোধহয় সঠিক মূল্যায়ন, কেননা আমরা জানি কোনো কোনো অঞ্চলে বৌদ্ধদের হত্যা করা হয়েছিল, এবং কোনো কোনো অঞ্চলে জৈনদের শূলে চড়ানো হয়েছিল। পরবর্তী সহস্রাব্দে, মানে গত কয়েক হাজার বছরে বিষয়গুলো খুব একটা বদলায়নি। উপনিবেশিক পণ্ডিতরা যেমন করে দেখিয়ে থাকেন এখানে তেমন ধর্মীয় আগ্রাসনের সংস্কৃতি ছিল না, আবার পুরোপুরি মুক্তও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ের দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের মতো এটি স্বাভাবিক সংস্কৃতি ছিল।
কিন্তু পূর্বেকার মতোন মধ্যযুগও এমন এক সময় ছিল যখন উল্লেখযোগ্য সৃজনশীলতা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল, এবং আমরা এটা মেনে নিয়েছি। সংস্কৃত, ফারসি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় যে বুদ্ধিবৃত্তিক সজীবতা প্রকাশ পেয়েছিল সেটা পূর্বের কালের সাথেও মিলে যায়, যদিও তা বিভিন্ন ঘরনায়। বর্তমানের জমিনে আমরা যা হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করি তা, পুরোপুরি না হলেও বহুলাংশ, মূলত ঐ সময়েই রূপ ও আকার ধারণ করেছিল।

বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মের সংস্কৃতির মধ্যকার মিথস্ক্রিয়াকে এই মুহূর্তের জন্য বাদ দিলেও, ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যের চতুর্দিকে এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ জড়ো হয়েছে যেগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক। গত একহাজার বছর জুড়ে, কাশ্মীর থেকে কেরালা পর্যন্ত ব্রাহ্মণীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় অনুশীলনের উপর বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাভাষ্য রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের সায়ানার ব্যাখ্যা হলো চতুর্দশ শতকের বিদ্বান পণ্ডিতের বাস্তব ও কল্পনার মিশেলের এক দুর্দান্ত নজির। সামাজিক পরিবর্তনই বিদ্যমান সামাজিক সংহিতাগুলোর নতুন নতুন ভাষ্য হাজির করেছিল। মনু ধর্মশাস্ত্রের কুল্লুকার ধারাভাষ্য তৎকালীন সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যেমন, ব্রাহ্মণদের অন্যান্য বর্গের সাথে মন্দিরের পুরোহিতদের অবস্থান কি হবে সে বিষয়ক তর্ক। এই তর্ক এমন এক সময়ের ছিল যখন মন্দিরগুলো খুবই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল, এবং পাশাপাশি উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটছে। কিছু কিছু সম্পদশালী মন্দির লুট একইসময়ে অন্যান্য আরো সম্পদশালী মন্দির নির্মাণে এবং সৃজনশীল স্থাপত্য উদ্ভাবনে বাধা হয়ে দাড়াতে পারেনি।
শাস্ত্রীয় সংস্কৃত কবিতা ও সাহিত্যের উপর বহু ভাষ্য, সারসংগ্রহ ও আলাপ-আলোচনা চালু ছিল। আঞ্চলিক ভাষার দিকে ধীরে ধীরে মোড় ঘোরানোর সাথে ব্যাকরণগুলোরও বিভিন্ন ভাষ্যের প্রয়োজন পড়েছিল। চতুর্দশ শতকে নতুন ও পুরাতন দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মাধবাচার্যের সর্ব-দর্শন-সংগ্রহতে আলোচনা করা হয়েছে। দর্শনের অদ্বৈত বেদান্ত ও মীমাংসা ঘরনার উপর আলাপ-আলোচনা এখনো চালু আছে। জ্ঞানবিজ্ঞানে ভারতীয় পণ্ডিতদের চূড়ান্ত মুহূর্তে গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যায় তত্ত্বের অন্বেষণ উজ্জাইন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মহারাজা ও মুঘলদের দরবার এবং ধনবানদের বাড়িগুলো ধ্রুপদী হিন্দুস্তানি ও কর্ণটিক সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।
সংস্কৃত ও ফারসির পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাগুলোতেও উঁচুদরের সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল, যা রাজ দরবারে এবং উপদলগুলোর সাথে সংযুক্ত স্থানে নতুন একটা অবস্থান অর্জন করেছিল। এই রচনাগুলো তাদের সময়ের চিন্তা ও সৃজনশীলতার অনেকটাই বহন করতো। যেমন দেখা যায় রামচরিতামানস এবং কৃত্তিবাসী-তে; এগুলো বাল্মীকির রামায়ণের থেকে স্বতন্ত্র এবং হিন্দি ও বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে খুব শ্রদ্ধেয়। এমনকি লোককবিদের মুখে মুখে এমন বিকল্প কাহিনী বা ইতিহাস ছড়িয়ে পড়তো যা আমাদের উদ্ধৃত দরবারী ইতিহাস থেকে অনেক আলাদা। এগুলো বিপুল সংখ্যক জনগণের কণ্ঠস্বর ছিল, যেমন করে মীরাবাঈ ও সুরদাসের ভজনা এবং ত্যাগরাজের গানে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো বন্দি বা দাস মানুষের অর্জন ছিল না। আমাদেরকে যারা উপনিবেশ করেছে, এবং যারা অনুগত হয়ে সেই উত্তরাধিকার বহন করে যাচ্ছেন তারা আমাদেরকে যা বলেছেন এর বাইরে দেখতে আজ আমরা অক্ষম।
সেকুলারকরণের কাজ
অতীতের কিছু কিছু দিকে নজর দেয়ার এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় আমি চেষ্টা করেছি ভারতে বিভিন্ন উপদলের আকারে এবং জাতপ্রথার সাথে এদের মিশেলে ধর্মের যে বহুত্ববাদী ভাষ্য হাজির আছে তার একটা রূপরেখা তুলে ধরা। অবশেষে নাগরিক সমাজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে নিষ্ক্রিয় করা আমাদেরকে আরোও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে সহায়তা করবে। সেকুলারকরণের প্রক্রিয়াটির জন্য ধর্ম ও বর্ণ উভয়কেই সম্বোধন করতে হবে এবং এ পর্যায়ে অন্য স্থানের ধর্মের থেকে ভিন্ন ধরণের বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আমাদের ধর্ম ও আমাদের সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের উপনিবেশিক সংস্করণকেই আত্তীকরণ (internalised) করেছি ফেলেছি, এবং এর পরিণতিতে প্রভাবশালী ধর্মীয় সংগঠনের কর্কশতা অনুভব করছি। এর মধ্যে কয়েকটিকে আমরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য হাতিয়ার হয়ে উঠার সুযোগ করে দিয়েছি। ফলে সেকুলারকরণের কথা আমাদেরকে সংবেদনশীল হয়ে, যতন সহকারে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করতে হবে। যদিও এটি দ্রুত পরিবর্তন করা যাবে না, তবু একটি সেকুলার সমাজের প্রতি আস্থা প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের সাথে এর প্রয়োজনীয় যোগসূত্রটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেকুলার মূল্যবোধগুলো প্রবর্তনের সূচনা করতে হবে। হত্যার মাধ্যমে সেকুলারবাদীদের নীরব করে দেয়ার প্রচেষ্টা কখনোই সফল হবে না- এটি কেবল ধীরে ধীরে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিবে যা একদিক তাদেরকেই আঘাত করবে যারা এখন অন্যের মনে ত্রাস সৃষ্টি করছে। ইতিহাস যদি আমাদের কোনো শিক্ষা দিয়েই থাকে তাহলে তা হচ্ছে এ-ই।
একটি সেকুলার সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা [পলিটি] মানে ধর্মকে ত্যাগ করা নয়। এর অর্থ হচ্ছে কোনো ভারতীয়ের ধর্মীয় পরিচয়, তা যাই হোক না কেন, প্রাথমিকভাবে ভারতীয় নাগরিকের সেকুলার পরিচয়েই সপে দিতে হবে। এবং এই পরিচয়ের সাথে সাথে যে অধিকারসমূহের প্রসঙ্গ আসে অর্থাৎ নাগরিক অধিকারসমূহ, তার নিশ্চয়তা রাষ্ট্রকে অবশ্যই দিতে হবে। এই যে দাবি, মানে রাষ্ট্র মানবাধিকার সরবরাহ করবে এবং সুরক্ষা প্রদান করবে, তা এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যাচ্ছে না। এটি এমন একটি পরিচয় যা মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে [সবার জন্য প্রযোজ্য] আইনের সেকুলার নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।
সম্ভাব্য দুটো উপায়ে এর সূচনা করা যেতে পারে। একটি হলো শিক্ষাক্ষেত্রে সেকুলার নিশ্চিত করা এবং অন্যটি হচ্ছে সেকুলার নাগরিক আইন। শিক্ষা মানে হচ্ছে কোনো বৈষম্য ছাড়া জ্ঞানের সকল শাখায় সকল নাগরিকের প্রবেশাধিকার। জ্ঞান মানে হচ্ছে হালনাগাদ তথ্য এবং পর্যালোচনামূলক জিজ্ঞাসার পদ্ধতি গ্রহণের জন্য তরুণদের প্রশিক্ষণদান। এর সাথে আমি নতুন প্রজন্মের জন্য অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা যুক্ত করতে চাই। কীভাবে আমাদের গণতন্ত্র সর্বোত্তম কাজ করতে পারে সেটা নিয়ে বোধহয় আমরা কাজ করতে পারি।
আমাদের নাগরিক আইনগুলো উপনিবেশিক সময়েই তৈরি হয়েছিল, যদিওবা স্বাধীনতার পর আমরা কিছু পরিবর্তন এনেছি। সেকুলারের দিকে মোড় নেয়ার জন্য, আমাদেরকে বিদ্যমান নাগরিক আইনগুলোকে সতর্কভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে যেন কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই এগুলো সকলের নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করে। নাগরিক আইন এবং প্রতিটি ধর্ম ও বর্ণের আইনকানুনের মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিরসনে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা করতে হবে। বর্তমানে যারা ধর্মীয় ও জাতের নীতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে কেবল তাদের সাথে বসলে হবে না। একটি অভিন্ন নাগরিক নীতির অর্থ এই নয় যে ধর্মীয় নীতির আইনকে সরিয়ে দেয়া। এর অর্থ হচ্ছে, সকল ধর্মীয় নীতির সামাজিক আইনকে যৌথভাবে পুনর্বিবেচনা করে একটি সাধারণ সেকুলার নাগরিক নীতিতে পৌঁছানো। এই প্রক্রিয়ায় যে কোনো ধরণের সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও বৈষম্যকে দূর করা দরকার। আইন তখন আর আইন থাকে না যদি একে কাজে লাগিয়ে বৈষম্যকেই মঞ্জুর করা হয়। সেকুলার সমাজের দিকে যাত্রার জন্য এটিই বোধহয় আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি মুশকিলের হবে। শুরু করার জন্য এখনই কি সময় নয়?
আমাদের চারপাশের দুনিয়ায় ধর্মভাবের [religiosity] যে দুর্বার প্রদর্শন – ধর্ম না কিন্তু, ধর্মভাবের অত্যধিক প্রদর্শন – দেখা যাচ্ছে তা কখনো প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা সমাধান করতে না পারার কারণে হতে পারে; অথবা আমাদের অনিশ্চিত নিরাপত্তাহীন একটি প্রতিযোগিতামূলক সমাজে পরিণত হওয়ার কারণেও এটা হতে পারে। এর বিপরীতে নাগরিকত্বের বাস্তবতাকে কীভাবে আমাদের সামাজিক কল্যাণ, মঙ্গল, দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া এবং জীবনে উৎকর্ষতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষার একটি গ্যারান্টি বানাতে পারি সে বিষয়ে কী বিবেচনা করতে পারি? সমাজকে সেকুলার বানানো কোনো রাতারাতি বিপ্লব সাধন নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং সময়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই রাষ্ট্র ও সমাজকে নতুন উপায়ে কাজ করানো দরকার- এর স্বীকৃতিটা একে সহায়তা করবে বলে আশাবাদী। গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের কর্মকাণ্ডের নৈতিক সমর্থন। সমাজের সেকুলারকরণ সেই নৈতিকতার এক অগ্রযাত্রা।